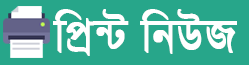
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই শিরোনাম: “দূর্নীতি রাষ্ট্রে নয়, মননে”। অর্থাৎ, দূর্নীতি সমাজ বা রাষ্ট্রের শীর্ষে নয়, বরং তা গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনায়, আমাদের মূল্যবোধে, আমাদের নৈতিকতার অভাবেই। এই প্রতিবেদনটি সেই দিকেই আলোকপাত করার প্রয়াস।
দূর্নীতি বলতে আমরা বুঝি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়মের ব্যত্যয়, অসৎ আচরণ, কিংবা অন্যায়ভাবে সুবিধা লাভের চেষ্টা। এটি শুধুমাত্র বড় কোনো অর্থ কেলেঙ্কারি নয়, বরং পরীক্ষায় নকল করা, লাইনের ধাক্কা দিয়ে আগে চলে যাওয়া, ট্রাফিক আইন ভাঙা কিংবা সৎ পথে না গিয়ে shortcuts খোঁজা—এসবও একেকটি দূর্নীতির রূপ।
তবে এই কাজগুলোর পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা কাজ করে, সেটি হলো — “আমি পারলে করবো”, “সবাই করছে”, “আমার না করলে চলবে না”। অর্থাৎ আমাদের মানসিক গঠনে এক ধরনের অবক্ষয় তৈরি হয়েছে যেখানে সততা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা গৌণ হয়ে গেছে।
দূর্নীতির গোড়া ধরা যায় পরিবারে, শিক্ষায় এবং সামাজিক চর্চায়। একজন শিশু যখন দেখে তার অভিভাবক ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করছে বা মিথ্যা বলছে, তখন সেও সেটিকে শিখে নেয় এবং সেটিই হয় তার মূল্যবোধের ভিত। একইভাবে, যখন একজন শিক্ষার্থী দেখেন পরীক্ষায় নকল করে কেউ ভালো ফল পাচ্ছে, আর সৎভাবে পড়েও পিছিয়ে পড়ছে—তখন তার মধ্যে অসততা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
অর্থাৎ, দূর্নীতির শিকড় রাষ্ট্রে নয়, বরং পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও সমাজের প্রতিটি স্তরে—আমাদের চিন্তায় ও চর্চায়।
রাষ্ট্রের কাঠামো ও ব্যক্তির মননের সংঘাত
প্রশাসনিক দূর্নীতি বা রাজনৈতিক দূর্নীতিকে আমরা প্রায়ই সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখি। অথচ সেই প্রশাসন বা রাজনীতি চালায় তো আমাদেরই মতো মানুষ। একজন রাজনৈতিক নেতা হঠাৎ করে দূর্নীতিবাজ হয়ে ওঠেন না; তিনি সমাজ থেকে শিক্ষা পান, পরিবারের ভিত থেকে উঠে আসেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় দূর্নীতির গোড়া সমাজে, সমাজের গোড়ায় ব্যক্তি—আর ব্যক্তির মননে। যদি ব্যক্তির মনন সৎ হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় স্তরে দূর্নীতিও হ্রাস পাবে।
কিছু সাধারণ উদাহরণ
১. দ্রুত সেবা পেতে ঘুষ দেওয়া: নাগরিক হিসেবে যখন আমরা ঘুষ দিয়ে নিজের কাজ আগে করিয়ে নিতে চাই, তখন আমরা নিজেরাই দূর্নীতিকে উৎসাহ দিচ্ছি।
২. ট্রাফিক আইন অমান্য করা: সিগন্যাল ভেঙে যাওয়া, হেলমেট না পরা, লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো—এসব আমাদের অসচেতন মননেরই প্রতিফলন।
৩. পরীক্ষায় নকল করা বা প্রশ্নফাঁস: ছাত্রজীবনের এই ছোট ছোট দুর্নীতিই ভবিষ্যতের বড় দুর্নীতির ভিত্তি গড়ে দেয়।
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রতিটি সমাজের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইসলামে, হিন্দুধর্মে, খ্রিষ্টধর্মে—সব ধর্মেই দূর্নীতিকে চরম অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন ও আত্মশুদ্ধির চর্চা যদি ব্যক্তি পর্যায়ে গড়ে ওঠে, তাহলে সমাজে দূর্নীতির স্থান কমে আসবে।
যেহেতু দূর্নীতির গোড়া ব্যক্তির মানসিকতা বা মননে, তাই সমাধানও সেখানেই শুরু হওয়া উচিত। এর জন্য দরকার:
১. নৈতিক শিক্ষার প্রসার: প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পাঠ্যসূচিতে নৈতিকতা, সততা ও দায়িত্ববোধ শেখানো।
২. পরিবারে সততার চর্চা: শিশুরা যেন তাদের বাবা-মায়ের আচরণ থেকে সৎ জীবনযাপনের শিক্ষা পায়।
৩. সমাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: ছোটখাটো অনিয়মকেও প্রশ্রয় না দিয়ে প্রতিবাদ করা এবং প্রতিবেশীকে সচেতন করা।
৪. মিডিয়া ও সংস্কৃতির ভূমিকা: টেলিভিশন, সিনেমা, সাহিত্য ইত্যাদিতে সৎ চরিত্র ও নৈতিক সংগ্রামের জয়গান তুলে ধরতে হবে।
দূর্নীতিকে যদি আমরা শুধু রাষ্ট্রের সমস্যা হিসেবে দেখি, তাহলে আমরা এর মূল উৎসকে উপেক্ষা করবো। কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে, এটি আমাদের চিন্তা, মনন, ও জীবনের চর্চা থেকে উদ্ভূত—তাহলে পরিবর্তন শুরু হবে আত্মজিজ্ঞাসা থেকে।
রাষ্ট্রকে শুদ্ধ করতে হলে আগে মননকে শুদ্ধ করতে হবে। তাই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে যে, রাষ্ট্র নয়—আমরাই রাষ্ট্র। মননের মধ্যে যখন সততা গড়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্রও দুর্নীতিমুক্ত হতে বাধ্য।
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ইস্টার্ন কলেজ
সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী


